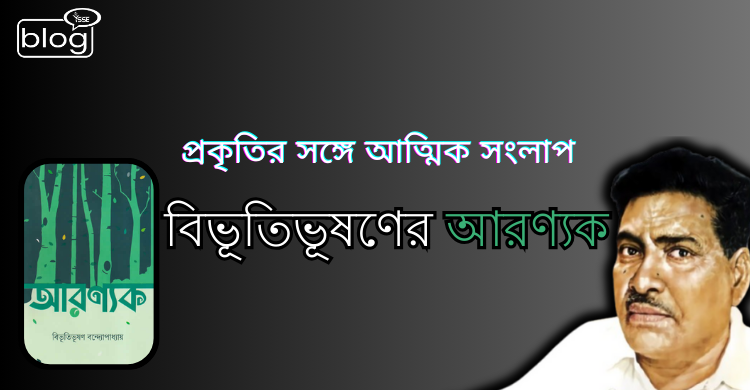“ মানুষ কি চায়—উন্নতি, না আনন্দ? উন্নতি করিয়া কি হইবে, যদি তাহাতে আনন্দ না থাকে?…
যাহারা জীবনে উন্নতি করিয়াছে বটে, কিন্তু আনন্দকে হারাইয়াছে। অতিরিক্ত ভোগে মনোবৃত্তির ধার ক্ষইয়া ক্ষইয়া ভোঁতা—জীবন তাহাদের নিকট একঘেঁয়ে, একরঙা, অর্থহীন—মন শান বাঁধানো, রস শেখানে ঢুকিতে পারে না।”
এ যেন সুপ্রিয় অরণ্যানীকে রক্ষা করতে না পারার সূক্ষ্ম বেদনার থেকে উদ্ভূত এক করুণ আর্তি, যেখানে পরাজিত আত্মার সমাধির উপর নগরসভ্যতার যে তাজমহল তৈরি হচ্ছে তার অন্তঃসারশূন্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে! বলছিলাম আজ থেকে ৮০ বছরেরও আগে ঠিক ১৯৩৯ সালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কালজয়ী আরণ্যক উপন্যাসের কথা!
উপন্যাসের শুরুতে বিভূতিভূষণ একটি দু-পাতার ভূমিকা বা প্রস্তাবনা লিখেছেন, তারপর মূল উপন্যাসটি ১৮টি পরিচ্ছেদে লেখা হয়েছে। বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম এক উজ্জ্বল নক্ষত্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাসিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে প্রধানতম হলো ‘আরণ্যক’। এটি বিভূতিভূষণের চতুর্থ উপন্যাস।
“সত্যচরণ” নামক একজন সরকারি কর্মকর্তার প্রান্তিক অঞ্চলে বদলি এবং তার শহরে জীবন বাদ দিয়ে অরণ্যের ভেতর বাস করা মানিয়ে নেওয়ার বর্ণনা নিয়ে মূলত এই উপন্যাসটি রচিত !
তবে সবমিলিয়ে নির্জন মায়াবী অরণ্যের বর্ণনা, সেখানকার হতদরিদ্র মানুষের জীবনসংগ্রাম, তাদের রোগ-শোক-আনন্দ-উচ্ছ্বাস-অভাব-আবেগ এবং বিভূতিভূষণের প্রগাঢ় জীবনদর্শনের সম্মেলনে আরণ্যক হয়ে উঠেছে মনের গহীনে বেঁচে থাকার মতো কালোত্তীর্ণ এক আখ্যান! সেই উপন্যাসের ই কিছু সারকথা নিয়ে আজ কথা বলবো!
এক.
‘আরণ্যক’ কোনো ভ্রমণকাহিনি বা ঠিক ডায়েরি নয়। কিন্তু উপন্যাসটি পড়তে গেলে কখনো কখনো সেরকমই লাগে। উপন্যাসটি জুড়ে আছে অরণ্যজীবনের অভিজ্ঞতাকে ঘিরে এক মুগ্ধতা। একজন শহুরে মানুষ হলেও খুব সহজভাবে বিশ্বাস করেন অরণ্য অঞ্চলের মানুষের লৌকিক ও অলৌকিক গল্পগুলিকে। এজন্যই উপন্যাসে উঠে এসেছে বিভিন্ন গল্প , যেমন : বন্য মহিষের দেবতা ‘টাড়বাড়ো’র কথা, একজন মহিলার রূপ বদলে কখনো ‘কুকুর’-এ পরিণত হওয়ার কথা বা রাতে জঙ্গলের মধ্যে হ্রদ ‘সরস্বতী কূণ্ডী’র কাছে পরীদের স্নান করার ঘটনা ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে তিনি অষ্টম পরিচ্ছেদে লিখেছেন,
“সেদিন আমার সত্যই মনে হইয়াছিল এখানে মায়াবিনী বনদেবীরা গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নাস্নাত হ্রদের জলে জলকেলি করিতে নামে। চারিধারে নীরব নিস্তব্ধ – পূর্বতীরের ঘন বনে কেবল শৃগালের ডাক শোনা যাইতেছিল।”
দুই.
বিভূতিভূষণের সৌন্দর্য-মুগ্ধতা ও তার অপূর্ব এক বর্ণনার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে এই উপন্যাসের বিভিন্ন স্থানে স্থানে! এই যেমন উপন্যাসটির পঞ্চম পরিচ্ছেদে আছে, একবার ফাল্গুন মাসে হোলির সময় মেলা দেখতে সত্যচরণকে কাছারিবাড়ি থেকে প্রায় দশ ক্রোশ দূরে একটি গ্রামে যেতে হয়। মেলা দেখে ফেরত আসার সময় বেশ ভালই বেলা হয়ে যায় কিন্তু সত্যচরণ কাছারিবাড়ি ফেরার জন্য উদ্যমী হয়। তখন তাকে রাতে জঙ্গলপথ ধরে ফেরার আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সবাই সাবধান করে। কিন্তু সে তা না মেনে চলে আসে। কিন্তু জঙ্গলের রাতের সৌন্দর্যের হাতছানি সে উপেক্ষা করতে পারে না, তাইতো তিনি লিখেছেন,
‘‘এ বাসন্তী পূর্ণিমার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নারাত্রে জনহীন পাহাড়-জঙ্গলের পথে একা ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়ার প্রলোভন আমার কাছে দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল।’’
প্রকৃতির এত রূপবৈচিত্র্যের সৌন্দর্যে পাগল হয়ে তিনি হয়তো একটু বাড়িয়ে বলেছিলেন যে- “আমার মনে হয় দুর্বলচিত্ত মানুষ যাহারা, তাহাদের পক্ষে সে-রূপ না দেখাই ভাল, সর্বনাশী রূপ সে, সকলের পক্ষে তার টাল সামলানো বড় কঠিন।’’
তিন.
সৌন্দর্য মুগ্ধতার সাথে সাথে উপন্যাসে বিভূতিভূষণের স্মৃতি কাতরতা ও যেন ফুটে উঠেছে, আর তার সঙ্গে জুড়ে আছে এক কল্পনার জগৎও। অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে,
‘‘এক-এক দিন বাংলা দেশে ফিরিবার জন্য মন হাঁপাইয়া উঠিত, বাংলা দেশের পল্লীর সে সুমধুর বসন্ত কল্পনায় দেখিতাম, মনে পড়িত বাঁধানো পুকুরঘাটে স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রে গমনরতা কোন তরুণী বধূর ছবি। মাঠের ধারে ফতফোটা ঘেঁটুবন, বাতাবিলেবুর ফুলের সুগন্ধে মোহময় ঘনছায়া ভরা অপরাহ্ণ।’’
চার.
উপন্যাসের কয়েক স্থানে সত্যচরণ বা বিভূতিভূষণের ইতিহাস-চেতনার ও বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে আছে,
‘‘পূর্বদিকের পাহাড়ের গায়ে একটা প্রকাণ্ড গুহা। গুহার মুখে প্রাচীন ঝাঁপালো বটগাছ। দিনরাত শন শন করে। দুপুর রোদে নীল আকাশের তলায় এই জনহীন বন্য উপত্যকা ও গুহা বহু প্রাচীন যুগের ছবি মনে আনে, যে-যুগে আদিম জাতির রাজাদের হয়ত রাজপ্রাসাদ ছিল এই গুহাটা, যেমন রাজা দোবরু পান্নার পূর্বপুরুষদের আবাস-গুহা। গুহার দেওয়ালে একস্থানে কতকগুলো কি খোদাই করা ছিল, সম্ভবত কোন ছবি – এখন বড়ই অস্পষ্ট, ভালো বোঝা যায় না। কত বন্য আদিম নরনারীর হাস্য-কলধ্বনি, কত সুখদুঃখ-বর্বর সমাজের অত্যাচারের কত নয়নজলের অলিখিত ইতিহাস এই গুহার মাটিতে, বাতাসে, পাষাণ প্রাচীরের মধ্যে লেখা আছে – ভাবিতে বেশ লাগে।’’
এছাড়াও, একাদশ পরিচ্ছেদে সাঁওতাল রাজা দোবরু পান্নার পূর্বপুরুষদের সমাধিস্থান ও দুর্গপ্রাসাদ দেখে সত্যচরণের কি ঐতিহাসিক উপলব্ধি হয়েছিল তা পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে বাঙালি পাঠকেরা জেনেছেন উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পর, এত বছর ধরে। এই গভীরতম অনুভবের প্রকাশভঙ্গি ই মূলত বিভূতিভূষণকে আলাদা করেছে তাঁর সমকালীন অন্য লেখকদের থেকে।
পাঁচ.
উপন্যাসের শেষে দেখা যায় সত্যচরণকে এই জমিদারির অধীন জমিগুলি বিক্রির বন্দোবস্ত করতে হচ্ছে, কিন্তু এই কাজটি তার মতো জঙ্গলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ মানুষের পক্ষে করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এই যে তাঁকে সৌন্দর্যে ভরা বিস্তৃত অরণ্যের এই জমি শেষমেশ বন্দোবস্ত করতে হয়, তার জন্য তিনি অনুতপ্ত মনে লেখেন,
‘‘হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়!
বিস্মৃতপ্রায় অতীতের যে নাড়া ও লবটুলিয়ার অরণ্য-প্রান্তর আমার হাতেই নষ্ট হইয়াছিল, সরস্বতী হ্রদের সে অপূর্ব বনানী, তাহাদের স্মৃতি স্বপ্নের মত আসিয়া মাঝে মাঝে মনকে উদাস করে।’’
উপন্যাসের শেষে সত্যচরণের এই আক্ষেপ ও অন্তর্বেদনা পাঠক মনেও সঞ্চার করে শূন্যতার অনুভূতি!
এরকম আরো ব্লগ পড়তে, ক্লিক করুন এখানে
লেখক
মাফরুহা সুমাইয়া
ইন্টার্ন , কন্টেন্ট রাইটিং ডিপার্টমেন্ট
YSSE