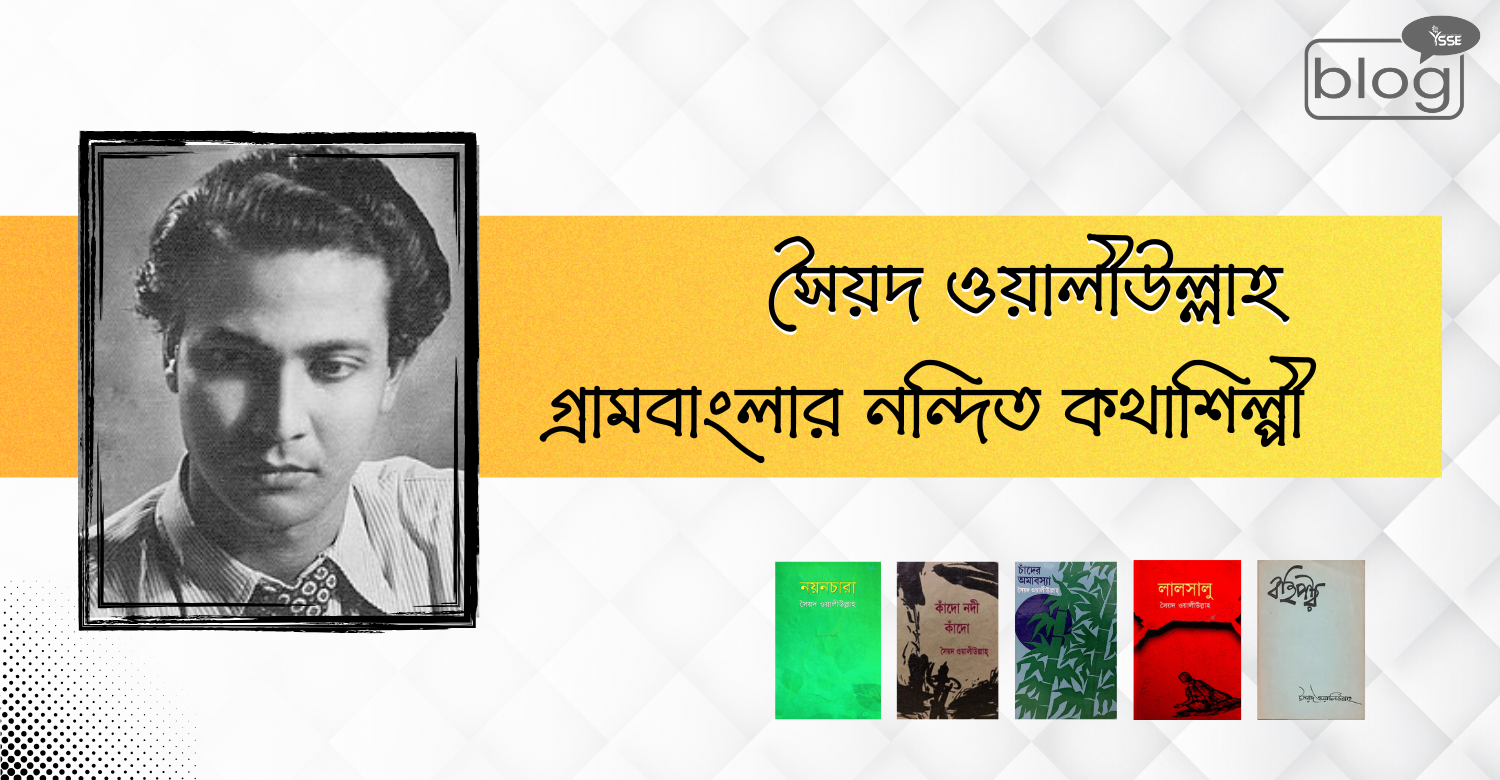সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১), বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় চরিত্র । তিনি গ্রামবাংলার জীবন, সংস্কৃতি, মানুষের অনুভূতি এবং সমাজের বিভিন্ন সমস্যাকে চিত্রিত করার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর সাহিত্যকর্মে গ্রামীণ সমাজের এক অতুলনীয় বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলেছেন, যা তাকে “গ্রামবাংলার নন্দিত কথাশিল্পী” হিসেবে বিশেষ পরিচিতি দিয়েছে।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯২২ সালের ১৫ জুন চট্টগ্রাম শহরের ‘ষোলশহর’এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট, তার ছোটবেলা কেটেছে বিভিন্ন জায়গায়। যা তাঁর মনে এবং সাহিত্যিক জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে । যদিও তিনি কম সময়ই গ্রামে কাটিয়েছেন, তবে সেই স্বল্প সময়ের গ্রামীণ পরিবেশ এবং গণমানুষের জীবনযাত্রা তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল।
সাহিত্যিক জীবন
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ’র সাহিত্যিক জীবনের শুরু হয় ১৯৪৮ সালে। তিনি প্রথমদিকে কিছু ছোটগল্প লিখেছিলেন এবং তা বিভিন্ন বাংলা সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। মাসিক সওগাত এর ফাল্গুন ১৩৪৯ সংখ্যায় ‘প্রকল্প’ এবং মৃত্তিকা পত্রিকার গ্রীষ্ম ১৩৫০ সংখ্যায় ‘তুমি’ নামে তার দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ‘খেয়া’ নামে তার একমাত্র প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৫০ বঙ্গাব্দে।
তাঁর সাহিত্যজীবন ছিল সংক্ষিপ্ত, এই সময়ে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র নয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ’র গল্পে জীবনের কঠিন বাস্তবতা এবং সাধারণ মানুষের অশান্তি এবং সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই সংগ্রাম যেমন ছিল তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, তেমনি ছিল মনের অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা এবং যন্ত্রণার।
তিনি ১৯৬১ সালে উপন্যাসের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ১৯৬৫ সালে আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (গল্পগ্রন্থঃ দুইতীর) এবং পি.এ.এন পুরস্কার (নাটকঃ বহিপীর) লাভ করেন।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ’র কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা-
১. নয়নচারা (১৯৪৪)
নয়নচারা তার প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ। এতে ৮টি গল্প ছিল যার প্রতিটিতে তিনি একটি সাধারণ, গ্রাম্য পরিবেশে মানব মনের জটিলতা এবং মানবিক দুর্বলতার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পগুলোর নায়কেরা উঠে এসেছেন একেবারে নিম্নশ্রেণির সাধারণ মানুষের কাতার থেকে। এই গ্রামীণ প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে লেখক মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং সমাজের নানা সমস্যার মধ্যে গহীন সম্পর্ক চমৎকারভাবে স্থাপন করেছেন।
২. লালসালু (১৯৪৮)
এটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ’র শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম হিসেবে সমাদৃত। প্রকাশের দীর্ঘ ১২ বছর পর ১৯৬০ সালের এপ্রিলে ঢাকা ‘কথাবিতান’ থেকে এর ২য় সংস্করণ বের হওয়ার পর উপন্যাসটি প্রথম পাঠক প্রিয়তা পায়। লালসালু উপন্যাসে গ্রামের অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মমনস্ক, বাঙালি মুসলমান সমাজের আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক দিক তুলে ধরা হয়েছে। এই রচনায় সেই সময়ের সমাজের অন্ধবিশ্বাস, কবরপূজা, এবং সামাজিক ভেদাভেদ চিত্রিত হয়েছে।
৩. চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪)
এটি তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য অস্তিত্ববাদী উপন্যাস, যেখানে তিনি মানব প্রকৃতির জটিলতা এবং জীবনযাত্রার অন্ধকার দিকগুলো চিত্রিত করেছেন। এটি ১৯৬৩ সালে রচিত হলেও ‘নওরোজ কিতাবিস্তান’ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। উপন্যাসটি মূলত আত্মকথন এবং মানুষের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছে । এই উপন্যাসটি অনুধাবন করায়, কীভাবে একজনের ব্যক্তিগত সংকটগুলো বড় ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় সংকটে পরিণত হয়।
৪. কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮)
কাঁদো নদী কাঁদো উপন্যাসটি ছিল সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ’র শেষ রচনা। এতে ছোট হাকিম মুহাম্মদ মুস্তাফার অন্তর্মুখী চেতনা ও কুমুরডাঙ্গার জনগোষ্ঠীর জীবন প্রবাহ সুনিপুনভাবে উঠে এসেছে। এখানে লেখক গভীরভাবে অনুভূতি, বাস্তবতা এবং মনের অন্ধকার দিকগুলোর ওপর আলোকপাত করেছেন। উপন্যাসটি মানবতা এবং আধ্যাত্মিকতার মধ্যে স্থাপনের মাধ্যমে সমাজের বহুবিধ সংকটকে চিহ্নিত করেছে।
গ্রামবাংলার নন্দিত কথাশিল্পী
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন এমন এক কথাশিল্পী যাঁর রচনা শুধু নগরের সীমাবদ্ধতায় আটকে থাকেনি, বরং তাঁর সাহিত্যে গ্রামবাংলার জীবন, সংস্কৃতি, মানবিক সম্পর্ক এবং সেখানে বাস করা সাধারণ মানুষের কঠিন সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। লালসালু বা নয়নচারা উপন্যাসগুলোর মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, একজন লেখক কেবল শহরের বা সভ্যতার জটিলতা নয়, বরং গ্রামবাংলার মাটির গন্ধ, সেখানে বসবাসরত মানুষের মুখাবয়ব এবং তাদের টানাপোড়েনও সাহিত্যিক ভাষায় তুলে ধরতে সক্ষম।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ শুধু গল্পকার বা ঔপন্যাসিক নন। তিনি ছিলেন একজন সফল মৌলিক নাট্যপ্রতিভাও। তার ‘বহিপীর’ (১৯৬০), ‘তরঙ্গভঙ্গ’ (১৯৬২), ‘সুরঙ্গ’ (১৯৬৪) নাট্যগ্রন্থে তার আশ্চর্য প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে। এসব নাটকে তিনি তার স্বকীয়তা ধরে রেখেছেন।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ’র লেখনী জীবনযাপন এবং মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক তৈরি করেছে। তিনি একেবারে গ্রামবাংলার চরিত্রগুলোর আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক দ্বন্দ্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন। গ্রামীণ সমাজের এই আভ্যন্তরীণ জটিলতাগুলো সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর গল্পের মাধ্যমে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে পাঠক একদম প্রকৃত গ্রাম বাংলার চিত্র খুঁজে পান। ‘লালসালু’কে বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক শামসুদ্দিন আবুল কালাম পূর্ববাংলার ‘সাহিত্যের প্রথম সত্যিকারের উপন্যাস’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।
তাঁর উপন্যাস নয়নচারাতে গ্রাম বাংলার মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছোট ছোট সংকটগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এখানে তিনি সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে তার লেখার মাধ্যমে অর্ন্তভুক্ত করেছেন এবং সেই মানুষের যন্ত্রণাকে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ কখনও কখনও চরিত্রের মধ্যে নিরবতা, বেদনাদায়ক অবস্থা, ক্ষুদ্র বিশ্বাসকে আলোকিত করে দেখিয়েছেন, যা তাকে অন্যদের থেকে অনন্য করে তুলেছে।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ’র সাহিত্যিক প্রভাব
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ’র বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিকের সূচনা করেছেন। তিনি শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের বা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর মানুষের কথা বলেননি, বরং তাঁর লেখনী সব সময় একাধারে সর্বজনীন ও চিরকালীন ছিল। তাঁর চরিত্রগুলো সমাজের নানা শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে, এবং তাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মাধ্যমে তিনি সমাজের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলা সাহিত্যের নন্দিত কথাশিল্পী, যাঁর রচনা বাঙালি পাঠকের অন্তরে চিরকাল থাকবে।
১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবর প্যারিসে এই কালজয়ী সাহিত্যিক মাত্র ৪৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য রত্ন, যিনি গ্রামবাংলার জীবন, মানবতার সংগ্রাম এবং সমাজের বিভাজনকে গভীরভাবে এঁকেছেন। তাঁর সাহিত্যে যেসব নৈতিক এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রাধান্য পেয়েছে, তা আমাদের চিরকাল প্রেরণা দেয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলা সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় নাম হয়ে থাকবেন।
এই ধরণের আরও লেখা পড়তে এখানে ক্লিক করুন।
লেখক
ফারদিন বিন আব্দুল্লাহ
ইন্টার্ন, কন্টেন্ট রাইটিং ডিপার্টমেন্ট,
YSSE